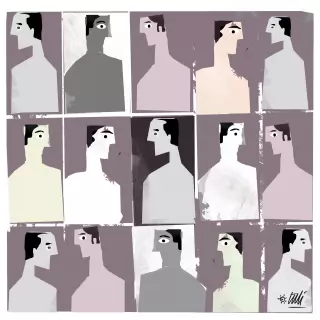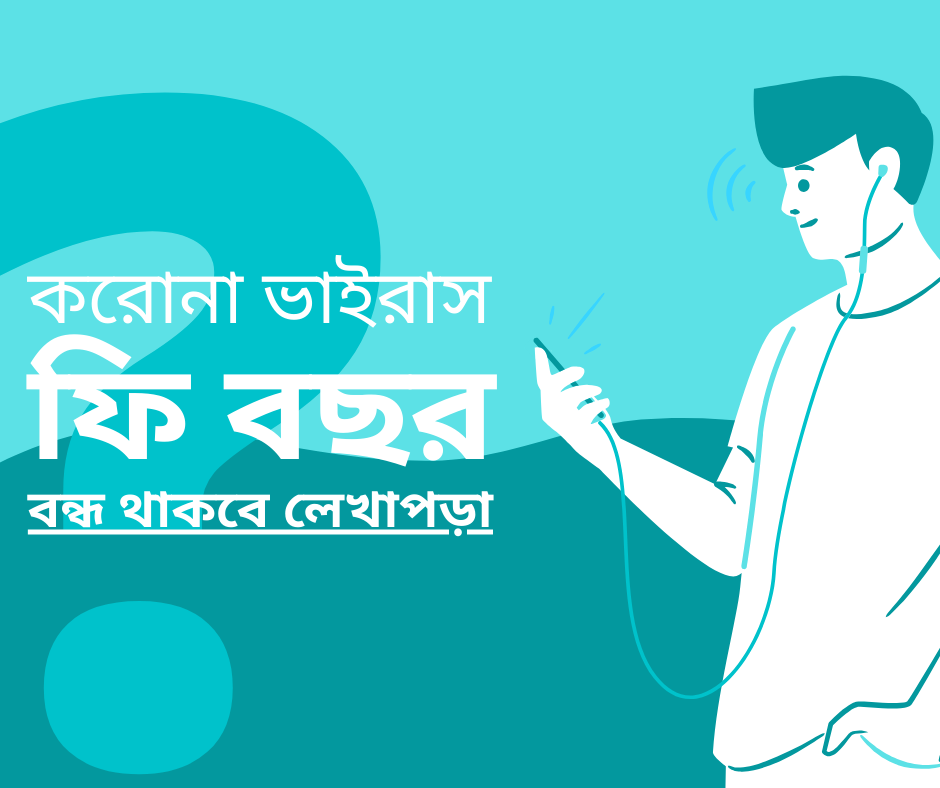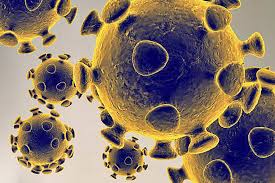গণতান্ত্রিক দেশে প্রধান রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে নানা রকম সভা-সমাবেশ-সম্মেলন করতে হয়। দলের কেন্দ্রীয় নেতারা নিয়মিত বৈঠক করেন। তাতে সমসাময়িক বিষয় আলোচনা করে প্রয়োজনবোধে বিবৃতি দেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা হয় কিছুদিন পরপর। তাতে দলীয় সাংগঠনিক বিষয় অথবা জাতীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর বাইরে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠক হয়। কিন্তু কোনো দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জাতীয় কাউন্সিল। জাতীয় সম্মেলনে দলের নেতৃত্বে পরিবর্তন আসে। অনেকে বাদ পড়েন, নতুন কেউ কেউ নির্বাচিত হন। শুধু নেতৃত্বে পরিবর্তন নয়, অনেক সময় দলের নীতি-আদর্শেও আসে পরিবর্তন। রাজনৈতিক দল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয় যে তার নীতি অপরিবর্তনীয়।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আগ্রহ অতি কম। আগ্রহ কেন কম, তার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা আছে, তবে মনস্তাত্ত্বিক কারণই প্রধান। সম্মেলন হলে নেতৃত্ব ও পদ হারানোর ভয় অনেককে আতঙ্কিত করে তোলে। ফলে যত দেরিতে জাতীয় সম্মেলন হয়, তত ভালো। পরিণামে দলীয় রাজনীতিতে দেখা দেয় স্থবিরতা। তার প্রভাব পড়ে জাতীয় রাজনীতিতে।
উপমহাদেশের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-তে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রতিবছরই জাতীয় সম্মেলন করত। প্রতিবারই সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পরিবর্তিত হতো। সেটা হতো গণতান্ত্রিক উপায়ে। গোপন ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে।
উপমহাদেশের দ্বিতীয় রাজনৈতিক দল নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দলও প্রতিবছর সম্মেলন করত এবং তাতে নেতৃত্বে পরিবর্তন আসত। নবাব সলিমুল্লাহ ছিলেন দলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ। গঠনের পর এক দশক তিনি জীবিত ছিলেন। এই সময়ও পালাক্রমে অনেকে লীগের সভাপতি ও সম্পাদক হয়েছেন।
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। অস্বাভাবিক প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এই দলের জাতীয় সম্মেলন কিছুটা দেরিতে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মাওলানা ভাসানীসহ দলের প্রধান নেতারা কারাগারে থাকায় যথাসময়ে সম্মেলন হতে পারেনি। ১৯৫৩-র নভেম্বরে প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন হয় ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে। এই সম্মেলনে ভাসানী পুনর্নির্বাচিত হন এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন শেখ মুজিবুর রহমান। দলের গঠনতন্ত্রে আনা হয় অনেক পরিবর্তন। দলের নাম থেকে ‘মুসলিম’ শব্দটি বাদ দেওয়ার কথা বলেছিলেন ভাসানী, কিন্তু সামনেই নির্বাচন বলে সোহরাওয়ার্দী পরামর্শ দেন সেটি বাদ না দিতে।
লীগের দ্বিতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৫-র অক্টোবরে। এটি ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন। এই সম্মেলন থেকে দলের নামে যে শুধু পরিবর্তন আসে, তা-ই নয়, নীতি-আদর্শেও আসে পরিবর্তন। দলের নাম হয় ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ’ এবং নীতি হয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা। এই সম্মেলনে আরও কিছু নীতি ও আদর্শগত পরিবর্তন আসে, যা পাকিস্তানের নিয়তি নির্ধারণ করে দেয় এবং বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের বীজ রোপণ করে।
আজ বাংলাদেশের একশ্রেণির মিডিয়ার কিছু কিছু শব্দ খুবই প্রিয়, যেমন ‘চমক’। তারা সবকিছুতেই ‘চমক’ দেখতে পায়। তারা দলের নির্বাচনী ইশতেহারে চমক দেখে, মন্ত্রিসভা গঠনের আগেই জনগণকে জানিয়ে দেয়: প্রস্তুত থাকুন, চমক আসছে। কাউন্সিল অধিবেশন হওয়ার মাস কয়েক আগে থেকেই প্রচার করতে থাকে, ‘চমক’ আসছে। বহু বছর যাবৎই এ রকম চমকিত করার প্রয়াস ও প্রচার চলছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষ চমকিত না
হয়ে বরং কিছুটা তাজ্জব হয়ে দেখে—এ তো সেই ‘থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়’, যাঁহা বায়ান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন।
স্বাধীনতার আগে প্রধান রাজনৈতিক দলের কাউন্সিল সম্মেলনে যে টাকা ব্যয় হতো, এখন কোনো দোকান মালিক সমিতির সভায় তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা ব্যয় হয়। আজ কোনো সংগঠনের সম্মেলনের কথা শুনলে ব্যবসায়ী ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের বুক কাঁপতে থাকে। সম্মেলন উপলক্ষে ব্যয় যদি হবে ৫০ কোটি, চাঁদা ওঠে এর কয়েক গুণ বেশি। রাজনৈতিক দলের অন্তঃসারশূন্য সম্মেলনে জাতীয় রাজনীতিতে কোনো গুণগত পরিবর্তন আসে না, অথচ চোখধাঁধানো জাঁকজমকে টাকা খরচ হয় বেশুমার।
স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের কাউন্সিল অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমাদের সব প্রতিষ্ঠান যেমন দুরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত্যুশয্যায়, কাউন্সিল সম্মেলনও হারিয়ে ফেলেছে তার গুরুত্ব। কাউন্সিলের প্রধান কাজ হলো দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের কর্মকাণ্ডের বিচার-বিশ্লেষণ। তাদের আমলনামা আলোচনা করা। সারা দেশ থেকে আসা কাউন্সিলরদের কাছে তাঁদের জবাবদিহি করা। তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের মেজবানি খাওয়ানোর জন্য কাউন্সিল হয় না।
কাউন্সিলের সভায় প্রতিনিধিরাই শক্তিশালী, কেন্দ্রীয় নেতারা নন। ডেলিগেটদের প্রশ্নের জবাব দিতে কেন্দ্রীয় নেতারা বাধ্য। আমাদের দেশে ডেলিগেটদের দুপয়সা দাম তো দেওয়া হয়ই না, যেন তারা প্রজা, কেন্দ্রীয় নেতারা জমিদার। অবশ্য কেন্দ্রীয় নেতাদের অবস্থানও শক্ত নয়। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দলের শীর্ষ নেতা ও কেন্দ্রীয় নেতারা সহকর্মী। কিন্তু অনেককাল থেকেই বঙ্গীয় রাজনীতিতে দলের কেন্দ্রীয় নেতারা প্রভাবশালী শীর্ষ নেতার অনুগত অডার্লির (আরদালি) ভূমিকা পালন করেন। নেতার হুকুম পালন করা ছাড়া তাঁদের নিজস্ব সত্তা বলে কিছু নেই। দলের অভিধানে ভিন্নমত বলেও কোনো শব্দ নেই।
বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাউন্সিল হয় না বলে নতুন নেতৃত্বও তৈরি হয়নি। নেতারা পদ হারানোর ভয়ে, মন্ত্রিত্ব খোয়ানোর আশঙ্কায় সারাক্ষণ তটস্থ থাকেন। সে জন্য কাউন্সিলে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমালোচনার সুযোগ নেই—স্তাবকতার দরজা অবারিত। সুবিধাবাদী নেতারা যোগ্যতরকে হিংসা করেন। তাঁকে দলের নেতৃত্ব থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে শীর্ষ নেতাকে প্রভাবিত করেন। কোন নেতার জনসমর্থন কতটা, দলের প্রতি আনুগত্য কতটা, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ নেতার আস্থাভাজন কে কতটা।
কাউন্সিলে সততার সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় সমালোচনা করার পরিবেশ না থাকায় তার প্রতিক্রিয়া হয় জাতীয় ও অন্যান্য নির্বাচনে। দলের সমর্থন না পেয়ে অনেকে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বিজয়ী হন। তাঁদের বিজয়ী হওয়া দলের নেতৃত্বের প্রতি আস্থাহীনতা। বিষয়টি গণতান্ত্রিক উপায়ে বিবেচনা না করে দেখা হয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি বেয়াদবি হিসেবে। তাঁদের করা হয় বহিষ্কার, যা অগণতান্ত্রিক আচরণের দৃষ্টান্ত। জনমতকে অবজ্ঞা করা।
দলের সভায় স্পষ্ট কথা বলার সুযোগ থাকলে কারও গোপনে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ থাকে না। চাটুকারদের দৌরাত্ম্য হয় কম। সুবিধাবাদীরা বিশেষ সুবিধা করতে পারেন না। ডেলিগেটরা কাউন্সিলে এসে বিরিয়ানির প্যাকেটে দাওয়াত খেয়ে ফিরে যান, কিছু শিখে যান না। গোপন ব্যালটে ভোট দিতে পারেন না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, শুধু হাততালি দিয়ে যান।
স্বাধীনতার পর থেকে যদি প্রধান দলগুলোর জাতীয় কাউন্সিল গণতান্ত্রিক উপায়ে হতো, তাতে যদি দলের ভুলভ্রান্তি পর্যালোচনা করা হতো, নেতারা জবাবদিহি করতেন, আত্মসমালোচনা করতেন, তাহলে বাংলাদেশের রাজনীতি আজ চোরাবালিতে আটকে যেত না। সম্ভবত দেশে অসাংবিধানিক শাসনও আসত না।
কোনো দেশের অব্যবস্থা ও অপশাসনের জন্য কোনো একক নেতাকে বা শুধু সরকারকে দায়ী করা যায় না। সরকারি দল ও সরকারের বাইরের অন্যান্য দলের নেতারা দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। তাঁদের অযোগ্যতা, মেরুদণ্ডহীনতা, অসততা, আপসকামিতা, সুবিধাবাদিতার যোগফল একটি দেশের অগণতান্ত্রিক অপশাসন। পর্দার আড়াল থেকে সরকারি আনুকূল্য উপভোগ করার প্রবণতা সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে ভেতর থেকে শেষ করে দেয়। এ জন্য যাঁরা সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাঁদের কর্তব্য দলের কাউন্সিলকে গণতন্ত্রসম্মতভাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, যাতে দলের নিচের দিকের প্রতিনিধিদের মতপ্রকাশের সুযোগ থাকে।
সৈয়দ আবুল মকসুদ: লেখক ও গবেষক